ঠাকুরমার ঝুলি গল্পের মূল বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ কর
ঠাকুরমার ঝুলি গল্পের মূল বিষয়বস্তু
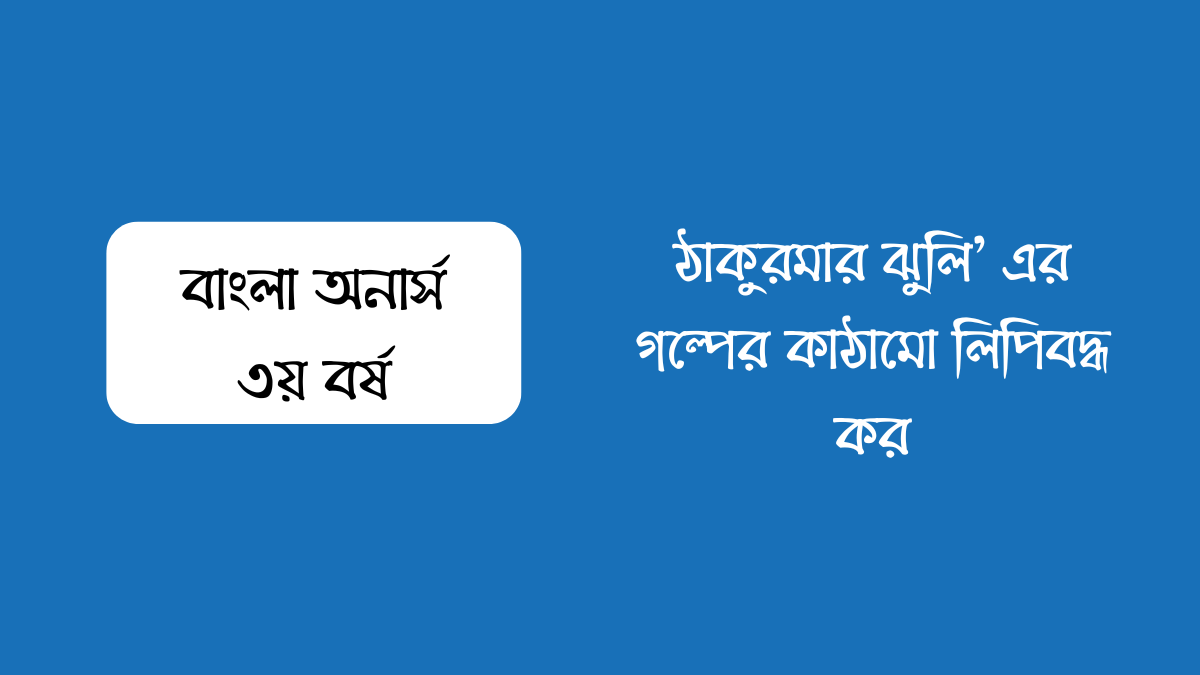 |
| ঠাকুরমার ঝুলি' এর গল্পের কাঠামো লিপিবদ্ধ কর |
উত্তর : গল্প বলার বা শোনার অভ্যাস মানুষের একটি চিরন্তন অভ্যাস। মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তি আদিমকাল থেকেই চলে আসছে। আদিমকাল থেকে শ্রুতিপরম্পরায় যে সকল বিষয়বস্তু চলে আসছে তা-ই গল্পের উপাদান।
কোন কোন গল্প বা রূপকথা রোমান্সধর্মী কল্পনা রাজ্যে স্বাধীনভাবে বিহার করে থাকে। আমরা ছেলে খেলায় গ্রামের বুড়োবুড়ি বা দাদা-দাদি বা নানা-নানির মুখে কোনো ঝিল্লিমুখর সন্ধ্যাকালে যেসব মনোহর ও চমকপ্রদ কাল্পনিক কাহিনি শুনতে শুনতে ঘুমিযে পড়েছি সেগুলোই রূপকথা।
যেমন আলী বাবা চল্লিশ দস্যু, আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ। রূপকথা আধুনিক গল্প উপন্যাস বা কথাসাহিত্যের আদিরূপ। দুটির উপাদান একই পার্থক্য শুধু কাঠামোগত বা প্রকাশভঙ্গির।
প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মুখে মুখে বা শ্রুতিপরম্পরায় যেসব কাহিনি চলে আসছে তাই হলো রূপকথা। কিন্তু আধুনিককালে রূপকথা বলতে শুধু সেসব কাহিনিকেই বুঝায় যা গদ্যে বিধৃত। তবে তা লিখিত বা অলিখিত ঐতিহ্যের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে স্থানান্তরিত হয়ে এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষে পৌঁছেছে।
অতএব আধুনিক সংজ্ঞানুযায়ী রূপকথা বলতে বুঝায় যা পুরুষ পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত সম্পদ এবং লিখিত বা মৌখিক গদ্যের বা পদ্যের ভাষায় প্রকাশ করা হয়ে থাকে। Fairy Tale বা Household Tale বলতে এমন বহুতর গল্পকে বুঝায় যে প্রায় সব কাহিনিই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।
রূপকথার মধ্যে যে শুধু পরীর গল্প থাকবে এমন কোনো কথা নেই।স্টিথ থম্পসন লোককথা বা রূপকথার সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে "Marchen হলো এক ধরনের কাহিনি যার নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য আছে আর আছে মটিফ বা অনুকাহিনির পরম্পরা।
এই কাহিনির ঘটনা ঘটে-অবাস্তব পৃথিবীতে যে পৃথিবীতে না আছে নির্দিষ্ট স্থান, না আছে নির্দিষ্ট চরিত্র, তদুপরি তা আশ্চর্য ব্যাপারে থাকবে পরিপূর্ণ। এই অসম্ভবের দুনিয়ায় নিরহঙ্কার নায়ক তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করে বাদশাহি পায় আর রাজকুমারীদের বিয়ে করে।
অতএব বলা যায়, রূপকথা হলো অবাস্তব পৃথিবীতে সংঘটিত সম্পূর্ণ অবাস্তব-কাল্পনিক বা স্বপ্নীল কাহিনি । দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের “ঠাকুর মার ঝুলির গল্পগুলোর আলোকে তার গল্পের কাঠামোগত দিক নিচে লিপিবদ্ধ করা হলো:দক্ষিণারঞ্জন মিত্র গল্পগুলোর প্রকাশ করেছিলেন ১৯০৭ সালে।
কিন্তু যখন তিনি এ গল্পগুলো সংগ্রহ করেছিলেন তখন তিনি গল্পগুলো প্রকাশ করার কথা ভাবেননি। তাই তিনি অনেকক্ষেত্রে লোকসাহিত্য সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে চলেননি । তিনি যতটা সম্ভব গল্পের ভাষাকে মৌখিক ভাষার কাছাকাছি রাখতে চেষ্টা করেছেন।
যেমন: 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে আমরা মৌখিক ভাষার প্রাধান্য দেখতে পাই। উদাহরণ :“এমন সময় কাহার আসিয়া আস্তে আস্তে ডাকিল, 'দাদা! দাদা!' রাজপুত্রেরা চুপি চুপি উত্তর করিল কে ভাই, কে ভাই? আমরা যে বুড়ীর পেটে।”
অথবা, “বাহির হইতে উত্তর আসিল “আমার লেজ ধর, আমার পুচ্ছ ধর!"তিনি শুধু গল্পের ভাষার ক্রিয়াপদকে কাঠামোর ক্ষেত্রে পরিবর্তন করতে পারেননি। কিন্তু শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেকটা মৌখিক ভাষার ব্যবহার করেছেন।
এ কারণে পরিবেশনের ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদকে অপরিবর্তিত রেখেছিলেন।দক্ষিণারঞ্জন মিত্র লোককথা, লোকগীতি প্রভৃতির কোন পরিবর্তন দেখাননি। যার প্রভাব আজও আছে। গানগুলোকে তিনি যতটা সম্ভব স্বকীয়তা বজায় রাখতে পেরেছেন। শিয়াল পণ্ডিত' এর আলোকে আমরা দেখতে পাই।
তিনি গানগুলোকে অবিকলভাবে তুলে ধরেছেন। যেমন-“তাক ডুম! ডুম ডুম!বেগুন ক্ষেতে ফুটল কাঁটা তাক ডুমা ডুম ডুম।কাঁটা খুলতে কাটল নাক,তাক ডুমা ডুম ডুনাকুর বদল নরুন পেলাম,তাক ডুমাডুম ডুম!”রূপকথায় যেমন কোন চরিত্রের নাম, কোন রাজার নাম বা কোন রানি বা রাজ্যের নাম পরিচয় পাওয়া যায় না।
তেমনি ঠাকুরমার ঝুলির গল্পগুলোর মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র গল্পের এ কাঠামো বজায় রেখেছেন। যেমন 'কলাবতী রাজকন্যাতে' আমরা দেখতে পাই- গল্পটি আরম্ভ হয়েছে এভাবে-"এক যে রাজা। রাজার সাত রানি- বড়রানি, মেজরানি, সেজরানি, ন-রানি, কনেরানি, দুয়োরানি আর ছোটরানি।
'আবার 'ঘুমন্তপুরী' গল্পে আমরা দেখতে পাই-একদেশের এক রাজপুত্র, রাজার পুত্রের রূপে রাজপুরী আলো। রাজপুত্রের গুণের কথা ধরে না।রূপকথার সবটুকু অংশ গদ্যে বলা হয় না আবার পদ্যেও বলা হয় না।
কারণ অধিকাংশ গল্পগুলো বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর জন্য Rythim হিসেবে ব্যবহৃত হতো। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র তাঁর অনেক গল্পে এই Form বা কাঠামো বজায় রেখেছেন। যেমন— 'কলাবতী রাজকন্যা'তে আমরা দেখতে পাই -“
কলাবতী রাজকন্যা মেঘ বরণ কেশঅথবা,তোমার পুত্র পাঠাইও কলাবতীর দেশআনতে পার মোতির ফুল ঢোল ডগরসেই পুত্রের বাদী হয়ে আসবে তোমার ঘর।না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর আগে আসুক রাজার বড় রানি, তবে দিব ফুল।”
রূপকথার গল্পগুলোর মধ্যে অনেক Type চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। গল্পগুলোর মধ্যে কামার, কুমার, ছুতোর, নাপিত চরিত্রগুলো আসবে তা যেন পূর্ব নির্ধারিত। শিয়াল, কুমির, বাঘ প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যায় রূপকথাতে এবং প্রতিটি টাইপ চরিত্র দ্বারা আলাদা আলাদা ভাব প্রকাশ করে।
যেমন রূপকথাতে শিয়াল চালাক বা মূর্ততার প্রতীক এবং কুমির বোকা প্রাণী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- 'শিয়াল পণ্ডিত' গল্পে আমরা দেখতে পাই-“ছেলেরা আজি ক খ পড়ে। শিয়াল বলিল কুমির মশাই দেখেন কি- সাতদিন যাইতে না যাইতেই আপনার এক এক ছেলে বিদ্যাজগতে ধনুধর হইয়া উঠিবে।
মহাখুশি হইয়া কুমির বাড়ি আসিল।"লোককথা বিশেষত রূপকথা ঐন্দ্রজালিক (Magical) ক্রিয়ার বিশেষ প্রাধান্য পায়। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র তাঁর গল্পের কাঠামো হিসাবে ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বজায় রেখেছেন। আমরা 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে দেখতে পাই-“রাজার মনে সুখ ছিল না।
কারণ- রানিরা সবাই নিঃসন্তান। একদিন রানিরা ঘাটে স্নান করতে গেছে এমন সময় এক সন্ন্যাসী বড় রানির কাছে একটি গাছের শিকড় দিয়ে বলল- এইটি বাটিয়া সাত রানিতে খাও, সোনার চাঁদ ছেলে হইবে।'গাছের শিকড় বাটা খাওয়া এবং সন্তান লাভ পুরনো লোকসংস্কার ও ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করেছে আলোচ্য গল্পটির মধ্যে।
অধিকাংশ রূপকথাগুলোতে সত্যের জয় এবং মিথ্যার পরাজয় দেখানো হয় এবং মিলনাত্মক পরিণতি পরিলক্ষিত হয়। “ঠাকুরমার ঝুলি' গল্পগুলোর মধ্যে কাঠামোগত সাদৃশ্য বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে দেখ যায়। যেমন ‘শীত বসন্ত’, ‘সাত- ভাই চম্পা', 'কিরণমালা' প্রভৃতি গল্পে এ আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।
যেমন-“রাজা এখনি বড়রানিদিগে হেঁটে কাটা উপরে কাঁটা নিয়া পুঁতিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিয়া, সাত রাজপুত্র পারুল মেয়ে আর ছোট রানিকে লইয়া রাজপুরীতে গেলেন। রাজপুরীতে জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল।"
(সাত ভাই চম্পা]রূপকথার সংলাপগুলোর মধ্যে নাটকীয়তা বিদ্যমান এবং এর সাথে আকর্ষিকতারও প্রাধান্য আছে। তবে এর মধ্যে ভাগ্য বা নিয়তিরও প্রাধান্য আছে। কেননা ঐ সময় মানুষের মধ্যে জাদুমন্ত্র বা সংস্কারের বিশ্বাস ছিল।
দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের অনেক গল্পে আমরা নাটকীয়তা এবং আকর্ষিকতা লক্ষ করি। যেমন: 'শীত বসন্ত' গল্পে বসন্ত যখন ধবল পাহাড়ের উপর দিয়ে ঝাপ দিয়ে নিচে পতিত হলো তখন আমরা লক্ষ করি-'অমনি ক্ষীর সাগর শুকাইয়া গেল, পদ্মের বন লুকাইয়া গেল।
দুধ বরণ হাতি-এক সোনার পদ্ম হইয়া জিজ্ঞাসা করিল- কোন দেশের রাজপুত্র কোন দেশে ঘর?'বসন্ত বলিলেন “বনে বনে বাস, আমি মুনির কোঙর।”দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের গল্পে কাঠামোগুলোর উপাদান অবাস্তব বলে মনে হয়েছে। কেনন। এর মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের ছোঁয়া নেই।
তবে গল্পগুলোর মধ্যে প্রাচীন সমাজের, প্রাচীন সভ্য সমাজের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তাছাড়া আধুনিক সমাজেরও কিছু ছোঁয়া আছে তাঁর গল্পগুলোর মধ্যে।
.webp)
